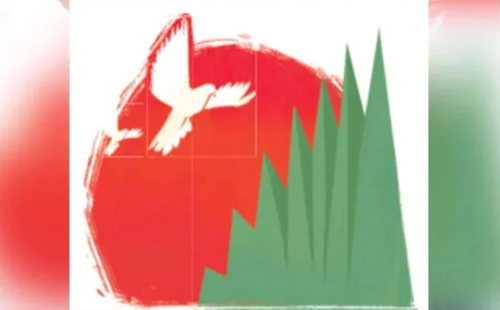সংবিধান যেভাবে বিভাজনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে

গত প্রায় ৫৪ বছরে বাংলাদেশ
রাষ্ট্রের অভিযাত্রায় দেখা যায়, আমাদের
সমস্যা শুধু অর্থনৈতিক, সামাজিক,
জনসংখ্যা বা আয়তনগত নয়,
রাজনৈতিকও বটে। সুনির্দিষ্টভাবে সেটা
হলো, সাংবিধানিক কাঠামোগত বিপত্তি। অন্তত ২০০ বছর ধরে
পৃথিবীতে নতুন রাষ্ট্রকাঠামো মূলত
গড়ে উঠছে লিখিত সাংবিধানিক
দলিলপত্রের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালের ১০
এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্য
দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের
রাষ্ট্রকাঠামো নির্মিত হয় ১৯৭২ সালের
সংবিধান দিয়ে।
তাৎক্ষণিক
প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রস্তুত সাধারণ
আইনের মতো করেই সংবিধানটি
পাস হয়। এতে এমন
একটি রাষ্ট্রকাঠামো নির্মিত হয়েছে, যাতে খুব সহজেই
নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে পুরো রাষ্ট্রটিকে নিয়ন্ত্রণ
করা যায়। ফলে অনেক
‘হুজুগে’ আর বিভক্তি সৃষ্টিকারী
মতাদর্শ সংবিধানে ঢুকে গেছে, যেগুলোর
কোনো দাবি বা প্রয়োজন
কিছুই ছিল বলে প্রতীয়মান
হয় না।
জাতীয়তাবাদ,
ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতন্ত্র—এই
তিন মূলনীতি জনবিভক্তির প্রধান উপাদান বলে দৃশ্যমান হয়েছে।
এর সঙ্গে রাষ্ট্রধর্ম, নাগরিকত্ব, রাষ্ট্রভাষা, জাতির পিতা/জনকের ধারণা,
আদিবাসী বনাম উপজাতি/ক্ষুদ্র
জাতিগোষ্ঠী ডিসকোর্স, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদি বিষয়ও রয়েছে।
পরিহাসের
বিষয় হলো, যে মুক্তিযুদ্ধের
চেতনা হওয়ার কথা ছিল জাতীয়
মতৈক্যের ভিত্তি, সেটাকেই জাতীয় বিভক্তির প্রধান হাতিয়ার বানানো হয়েছিল শেখ হাসিনার গত
১৫ বছরের শাসনামলে।
জাতীয়তাবাদ
অধ্যাপক
আনিসুজ্জামানের আত্মজীবনী বিপুলা পৃথিবী থেকে জানা যায়,
কীভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে অনুপ্রবেশ করে। তিনি লিখেছেন,
‘ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখে (১৯৭২)
রাষ্ট্রীয় সফরে বঙ্গবন্ধু গেলেন
কলকাতায়। সেখানে তিনি অভূতপূর্ব সংবর্ধনা
পেলেন। কলকাতার জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদ কথাটা যোগ করলেন তিনি।’
আনুষ্ঠানিকভাবে
প্রথম যে দলিলে আমরা
‘মুক্তিযুদ্ধের চার মূলনীতি’ বলে
দাবিকৃত জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের উল্লেখ
পেয়েছি, তা হলো, ১৯৭২
সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদে
উত্থাপিত ‘স্বাধীনতা ঘোষণা-সম্পর্কিত প্রস্তাব’।
জাতীয়তাবাদকে
রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে রাখার ব্যাপারটা কতটা যৌক্তিক, তা
নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ, বর্তমানে এটাকে তেমন উচ্চ মতাদর্শ
বলে গণ্য করা হয়
না।
বাঙালিরা
সিংহভাগ হলেও অন্য অনেক
জাতিসত্তার মানুষ এই বাংলাদেশে বাস
করে। যেকোনো আন্দোলন-সংগ্রামের সময়ই বৃহত্তর ঐক্য
তৈরির জন্য প্রায়ই জাতীয়তাবাদসহ
বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ভাষা, সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচয় প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু
রাষ্ট্রগঠনের সময় দরকার হয়
অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচয়কাঠামোর। তাই সংবিধান প্রণয়নের
সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয়তাকে পরিহার করে দেশের নামকে
প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল।
সংবিধানের
এই ‘আদি ভুল’ পরে
জিয়াউর রহমানের আমলে পরিবর্তন করা
হয়। এতে আমাদের নাগরিকত্ব
‘বাংলাদেশি’ বলে সাব্যস্ত হয়।
পঞ্চদশ সংশোধনীতে শেখ হাসিনার সরকার
‘বাংলাদেশি’ নাগরিকত্বের ধারণার ন্যায্যতা স্বীকার করে তা বহাল
রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু পঞ্চদশ
সংশোধনীতে স্বভাবসুলভ গোঁজামিলের পথে হেঁটে ‘বাংলাদেশের
জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী
এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন’—এমন একটি উদ্ভট
কথা সংযোজন করা হয়। এতে
মতাদর্শিক বিভক্তি পুনরায় ফিরে আসে।
এই মতাদর্শিক বিভক্তির ফলাফল চট করে বোঝা
বেশ দুরূহ। পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন
জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এবং বিহারিদের সঙ্গে
বাঙালিদের বর্ণবাদী আচরণ ও আধিপত্য
বিস্তার এই মতাদর্শিক বিভক্তির
ফলাফল। অন্যদের অধস্তন করে রাখার নিরন্তর
প্রচেষ্টা থেকে বাঙালি জাতিবাদের
স্বরূপ অনেকটাই দৃশ্যমান হয়।
জাতীয়তাবাদের
মতো ‘প্রায় বর্ণবাদী’ একটি মতাদর্শকে রাষ্ট্রীয়
মূলনীতি হিসেবে রাখা তাই ন্যায্য
ও প্রগতিশীল বলে মনে হয়
না, বরং বৈষম্যমূলক বলেই
প্রতীয়মান হয়। আমাদের রাষ্ট্রগঠনের
প্রথম দলিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের
কোথাও বাঙালি জাতির বা বাঙালি জাতীয়তাবাদের
কথা নেই; আছে ‘বাংলাদেশের
জনগণ’ (পিপলস অব বাংলাদেশ)।
ধর্মনিরপেক্ষতা
ও সমাজতন্ত্র
সংবিধানে
ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বিপুলা পৃথিবী বইয়ে লেখেন, ‘সংবিধানের
বিষয়ে পরামর্শ দিতে বঙ্গবন্ধু দুবার
ডেকে পাঠিয়েছিলেন কামালকে (ড. কামাল হোসেন),
সঙ্গে আমিও ছিলাম। তাঁর
প্রথম বক্তব্য ছিল রাজনীতির সঙ্গে
ধর্মের সংযোগ ছিন্ন করার একটা বিধান
থাকতে হবে সংবিধানে। ১২
অনুচ্ছেদে এ-বিষয়ে কিছুটা
বলা হয়েছিল, তবে বঙ্গবন্ধু যা
চেয়েছিলেন, তা সংবিধানের ৩৮
অনুচ্ছেদের শর্ত অংশে (ধর্মভিত্তিক
রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয় এর
মাধ্যমে) রূপ পেয়েছিল।’
ধর্মনিরপেক্ষতা
ও সমাজতন্ত্রকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বলার সুযোগ নেই;
বড়জোর যুদ্ধ-পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার তথা
মুজিবের রাষ্ট্রদর্শন বলা যেতে পারে।
বাস্তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে একত্রে
‘মুজিববাদ’ বলা হয়েছিল। খোন্দকার
মোহাম্মদ ইলিয়াসের মুজিববাদ বইয়ে সেটা শেখ
মুজিবুর রহমান নিজেও স্বীকার করেন।
সেই
বইয়ে শেখ মুজিবকে উদ্ধৃত
করে বলা হয়, ‘আমি
মনে করি, বাংলাদেশকেও অগ্রসর
হতে হবে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ,
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—এই
চার মূল সূত্র ধরে,
বাংলাদেশের নিজস্ব পথ ধরে। আমার
উপরিউক্ত মতবাদকে অনেকে বলছেন ‘মুজিববাদ”।’
ধর্মনিরপেক্ষতার
‘ধ্বজাধারী’ ভারতের সংবিধানেও তা শুরুতে ছিল
না। ভারতে জরুরি অবস্থা চলাকালে ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা
গান্ধী সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী এনে
প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই ক্ষমতা কুক্ষিগত
করার বেপরোয়া চেষ্টায় ইন্দিরা সংবিধান ‘পুনর্লিখন’ করতে চেয়েছিলেন।
প্রস্তাবনা,
৪০টি অনুচ্ছেদ, একটি তফসিল সংশোধন
এবং ১৪টি নতুন অনুচ্ছেদ
যুক্ত করায় একে অনেক
সমালোচক ‘কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া’র
পরিবর্তে ‘কনস্টিটিউশন অব ইন্দিরা’ বলা
শুরু করেন। জনদাবি না থাকলেও ব্যক্তি
ইন্দিরার খামখেয়ালিপনায় যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ভারতীয়
সংবিধানে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি জন-অভিপ্রায় ছাড়াই এগুলো আমাদের সংবিধানে যুক্ত করেন শেখ মুজিব।
ইন্দিরা
বা শেখ মুজিব—কে
যে কার ভাবনা ধার
নিয়েছেন, বোঝা দুষ্কর। তবে
দুজনেই যে ভারতীয় গণপরিষদের
সদস্য খুশাল তালাক্সি শাহর থেকে অনুপ্রাণিত
হয়েছিলেন, কেউ কেউ এমনটা
অনুমান করেন। খুশাল ১৯৪৮ সালে দু-দুবার ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ভারতীয়
সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন।
কিন্তু বি আর আম্বেদকরের
বিরোধিতায় সফল হননি।
শেখ
মুজিব সরকারের একমাত্র ম্যান্ডেট ১৯৭০-এর নির্বাচন। ছয় দফাই ছিল সেই নির্বাচনের মেনিফেস্টো। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র—কোনোটাই তাতে ছিল না। এতে ছিল, ফেডারেল রাষ্ট্র ও সর্বজনীন ভোটে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া সব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকা, দুই পাকিস্তানের জন্য পৃথক অথচ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা; কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকা, উভয় অঞ্চলেরই বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকার থাকা ও পূর্ব পাকিস্তানে স্বতন্ত্র প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠন করা।
আম্বেদকর
বলেছিলেন, সংবিধান হলো রাষ্ট্রের বিভিন্ন
অঙ্গের কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের প্রক্রিয়ামাত্র; ব্যক্তিবিশেষ বা দলকে ক্ষমতায়
বসানোর প্রকল্প নয়। রাষ্ট্রের নীতি
কী হবে, সমাজ কীভাবে
তার প্রতিবেশ আর আর্থিক পরিমণ্ডলে
সংঘবদ্ধ হবে, সেটা নির্ধারণের
এখতিয়ার তাদেরই। স্থান-কাল বিবেচনায় সেটা
তাঁরাই ঠিক করবেন। এগুলো
সংবিধানে খোদাই করার জিনিস নয়।
করলে, তা হবে গণতন্ত্রকে
হত্যার শামিল। মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে
ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শিক
বিধিবিধান রাখা, আইনসভা ও সরকারের ওপর
এসব বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দেওয়ার
কারণে এ প্রস্তাব বাহুল্য
বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
বাংলাদেশের
সংবিধানের দিকে তাকালেও একই
অবস্থা দেখি। এখানেও ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাশ্রিত
বিধান ২৭-২৯, ৩৪,
৩৮, ৪১, ৪২ অনুচ্ছেদের
মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৩-২০ অনুচ্ছেদগুলোতে
ছিল। ফলে মূলনীতি হিসেবে
ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র যুক্ত
করা বাহুল্যই ছিল।
১৯৪৮
সালের ভারতে আম্বেদকরের ঔচিত্যবোধ, দূরদৃষ্টি, গণতান্ত্রিক মানস জয়যুক্ত হলেও
১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বিজয়
হয় খামখেয়ালিপনা আর ব্যক্তিবিশেষের মতাদর্শ
রাষ্ট্রগঠনের মূল দলিলে প্রবিষ্ট
করার চেষ্টা। বাহাত্তরের সংবিধানকে অনেকেই যে ‘মুজিববাদী সংবিধান’
বলেন, সেটা তাই একদমই
ভিত্তিহীন নয়।
শেখ
মুজিব সরকারের একমাত্র ম্যান্ডেট ১৯৭০-এর নির্বাচন।
ছয় দফাই ছিল সেই
নির্বাচনের মেনিফেস্টো। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র—কোনোটাই তাতে ছিল না।
এতে ছিল, ফেডারেল রাষ্ট্র
ও সর্বজনীন ভোটে সংসদীয় সরকার
প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া
সব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকা, দুই
পাকিস্তানের জন্য পৃথক অথচ
বিনিময়যোগ্য মুদ্রা; কর ধার্য ও
আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকা, উভয়
অঞ্চলেরই বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকার থাকা ও পূর্ব
পাকিস্তানে স্বতন্ত্র প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠন করা।
মওলানা
ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে শিক্ষার্থী-জনতার যে গণ-অভ্যুত্থানের
ভেতর দিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র
মামলা থেকে শেখ মুজিবকে
মুক্ত করে আনা হয়,
তাতে ঘোষিত ১১ দফাতেও জাতীয়তাবাদ,
ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ছিল না। যে
‘লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার, ১৯৭০’ (এলএফও) মেনেই ’৭০ সালের নির্বাচনে
আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেছিল,
তাতে নির্বাচনে জয়ী দল পাকিস্তানে
একটি সাংবিধানিক ইসলামি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তানের সৃষ্টির ভিত্তি ইসলামি ভাবাদর্শকে রক্ষা এবং একজন মুসলিমকেই
রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করতে বাধ্য ছিল।
মূলনীতি হিসেবে ইসলামি জীবনবিধানের প্রচার-প্রসার, মূল্যবোধের পালন এবং কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন
না করাকে পাকিস্তানের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতেই হতো।
যেসব
ভাবাদর্শ সংবিধানে যুক্ত করা প্রয়োজন বা
জনরায় ছিল না, সেগুলো
অন্তর্ভুক্ত করার পাল্টা প্রতিক্রিয়া
হিসেবে পরে প্রস্তাবনায় ‘বিসমিল্লাহ’,
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা
ও বিশ্বাস’ এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের
অন্তর্ভুক্তির কারণ হিসেবে কাজ
করেছে—কেউ কেউ এমন
যুক্তি দেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবাদর্শ
ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করার বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ
মুসলিম অধ্যুষিত দেশের কারও কারও মনে
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল বলেই প্রতীয়মান হয়।
অধ্যাপক
আনিসুজ্জামানের বিপুলা পৃথিবী বই থেকে এর
কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়,
‘১২ অনুচ্ছেদের বিধান নিয়ে শাসনতন্ত্র কমিটিতে
বেশ বিতর্ক হয়েছিলো। চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর সম্পাদক মোহাম্মদ খালেদ এবং আরো দু-একজন সদস্য কথাটা
উঠিয়েছিলেন। তাঁরা বেশ জোরের সঙ্গেই
বলেছিলেন যে, মুসলমান হিসেবে
তাঁরা এক অখণ্ড জীবনবিধানের
অধীন—সেখানে ধর্ম ও রাজনীতিকে
পৃথক করা চলে না,
তাঁদের রাজনৈতিক জীবনও ধর্মবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত। তার অর্থ অবশ্য
এই নয় যে, বাংলাদেশকে
তাঁরা ধর্মীয় রাষ্ট্ররূপে দেখতে চান। বাংলাদেশে পালিত
ধর্মের মধ্যে রাষ্ট্র কোনো পক্ষপাত করুক
কিংবা ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্র কোনো পক্ষপাত করুক
কিংবা ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের মধ্যে কোনো বৈষম্য ঘটুক,
তা তাঁদের অভিপ্রায় নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয়
বিষয়ে যেমন, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে—তাঁরা ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারাই পরিচালিত হতে চান। শেষ
পর্যন্ত অবশ্য অধিকাংশের মত তাঁরা মেনে
নিয়েছিলেন।’
এই বিতর্ক গণপরিষদেই শেষ হয়নি, ধূমায়িত
হয়ে ছিল জনপরিসরে। ১৯৭৫
সালে বাকশালের পতনের পর পরবর্তী সময়ে
ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে ‘বিসমিল্লাহ’
এবং ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা
ও বিশ্বাস’ স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষ থেকে এগুলো
নিয়ে কোনো বাধা আসেনি।
পরে স্বৈরশাসক এইচ এম এরশাদ
ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করলেও একই রকমের প্রতিক্রিয়া
পাওয়া যায়।
ইসলাম
রাষ্ট্রধর্ম হওয়ায় জনতুষ্টি ছাড়া অবশ্য বাস্তব
কোনো অর্জন হয়নি। রাষ্ট্রধর্মের অনুসারী মুসলমানদের জন্য চাকরিতে কোনো
কোটা বা বাড়তি সুবিধা
দেওয়া হয়নি; বরং পাহাড়ি জনগোষ্ঠী,
মুক্তিযোদ্ধা, জেলা, নারী ইত্যাদি একান্তই
ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়ের জন্যই চাকরি/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোটা সংরক্ষিত ছিল।
২০১১ সালে শেখ হাসিনার
সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা
ও বিশ্বাস স্থাপন’কে মূলনীতি থেকে
বাদ দেয়; কিন্তু ‘বিসমিল্লাহ’
ও ‘রাষ্ট্রধর্ম’ বহাল রাখে।
শেষ
কথা
বর্ণবাদী
ও আধিপত্যকামী বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আলটপকা যুক্ত হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতা ও
সমাজতন্ত্রের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশে একটি মতাদর্শগত বিভাজন
জারি রেখেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের সন্তুষ্ট রাখতে একদিকে বহাল রাখা হয়েছে
‘বিসমিল্লাহ’ ও ‘রাষ্ট্রধর্ম’; অন্যদিকে
জনগণের অপর অংশের মধ্যে
সঞ্চারিত ক্ষোভের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুলা হিসেবে ঝুলিয়ে
রাখা হয়েছে। বিবদমান দুই পক্ষের কাছে
ত্রাতা হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার এই সুযোগ তৈরি
করেছিলেন শেখ হাসিনা। এভাবে
মতাদর্শিক প্রতারণার মাধ্যমে জনগণের দুটি অংশকে রণংদেহী
অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া
হয়।
২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান
আমাদের নতুন বাংলাদেশ গঠনের
একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। ইতিমধ্যে
সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। তাতে মতাদর্শিক বিভাজন
ঘটায়, এমন কিছু বিষয়
পুনর্মূল্যায়নের সুপারিশ এসেছে। বিভক্তি এবং বিভাজন সৃষ্টিকারী
মতাদর্শিক বিষয়গুলো ভবিষ্যতে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে না—এটাই
আমাদের প্রত্যাশা।